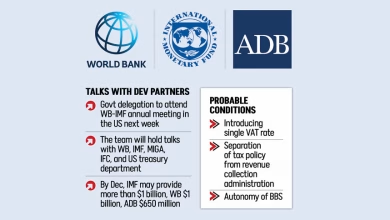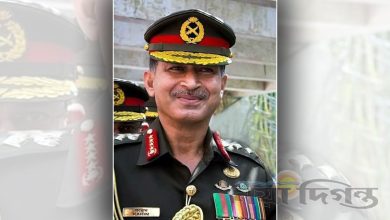আসল সংস্কার জনগণই করেছে

গণ-অভ্যুত্থানের আগের বছরটিতে বাংলা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটা বিদ্বেষের মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে সবাই সবাইকে ‘বাঙ্গু’ হিসেবে উপহাস করছেন। বাঙ্গু বাম, বাঙ্গু ডান, বাঙ্গু বুদ্ধিজীবী, বাঙ্গু বিপ্লবী, বাঙ্গু কী না!
জাতির অন্তরের গভীরে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছিল, যার বহিঃপ্রকাশ ছিল ওই প্রবল আত্মমর্যাদার, সবাইকে তুচ্ছজ্ঞান করার, হেয় করার ছোঁয়াচে উপসর্গ। সম্ভবত এর মধ্যেই ছিল সমকালীন রাষ্ট্রীয় অচলায়তনকেই যে নড়ানো যাচ্ছে না, তার কোনো সংস্কারই আর সম্ভব না; সেই রাজনৈতিক হতাশার একটা যৌথ মনস্তাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবি। হাসিনার অপরাজেয়তার অসচেতন এক স্বীকৃতিও, হাসিনার সরকারকে কেউ নাড়াতে পারবে না—কাজেই সব তত্ত্ব, মতাদর্শ, রাজনীতিই বৃথা। সবাই হাস্যকরভাবে পর্যুদস্ত। অতএব, সবাই বাঙ্গু।
অদ্ভুত একটা বিষয়, গণ-অভ্যুত্থানের পুরো সময়টায় কাউকে বাঙ্গু বলতে দেখিনি। গত বছরের ১৬ জুলাই আমার এই বিস্ময়ের প্রকাশটা ছিল এমন: ‘জাতি শ্রদ্ধা অর্জন করে। দেখো, গত এক সপ্তাহে কেউ কাউকে বাঙ্গু বলেনি। কারণ, ওইটা ছিল আমাদের নিজেদের ভেতর নিজেদের অসম্মান। আমরা নিজেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, তাই আমরা নিজেদের কাছে বাঙ্গু হয়েছিলাম। একজন আরেকজনের দিকে আঙুল তুলে নিজের প্রতি ওই তিক্ততাকেই ঘৃণা আকারে ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম। কিছুটা বিশ্বাস জন্মাচ্ছে, অনেকটা ভালোবাসতে পারছি একজন আরেকজনকে।’
একটা গণ-অভ্যুত্থান যে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে নিজেদের প্রতি, বিপ্লবে পরিণত হতে পারলে তা বহু ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় দেশকে। একেকটা সংস্কার ক্লেদের, অমর্যাদার একেকটা নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলে, একেকটা সংস্কার আশাবাদ আর আত্মবিশ্বাস তৈরি করে।
ঠিক এক বছরের মাথায় সংস্কার নিয়ে লিখতে বসে দেখলাম, চব্বিশ বিপ্লব নাকি অভ্যুত্থান—সেই বিতর্ক চলেছে বহুদিন। আর এখন আলাপ দাঁড়িয়েছে ন্যূনতম কতটা সংস্কার হলে আমরা খুশি!
জাতি কি আবার আত্মগ্লানির বিষাক্ত বাঙ্গুযুগে প্রবেশ করবে?
২.
গণ-অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ের বিবেচনায় সংস্কার দুই ধরনের হতে পারত—
ক. যেসব সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকার নিজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম।
খ. সংবিধান সংস্কারের মতো বিষয়গুলো, যা নির্বাচিত সংসদ ছাড়া সম্ভব নয়।
দুই ধরনের সংস্কারের গুরুত্বের তুলনা চলে না। উভয়ই অপরিহার্য।
গণ-অভ্যুত্থানের যদি একটি নির্ধারক শক্তি থাকত, তাহলে অন্তর্নিহিত শক্তির গুণেই নিজস্ব রাষ্ট্রদর্শন অনুযায়ী দুই ধরনের সংস্কারই শুরু হতে পারত। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান যতটা ছিল বিগত সরকারের প্রতি জনতার ক্রোধের প্রকাশ, এর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি ততটা ছিল না। সে কারণেই সংস্কারের ভাগ্য ঝুলেছে দোদুল্যমান ও আত্মবিশ্বাসহীন এবং ভাগ্যক্রমে ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপের ওপর।
নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সজাগ থাকলে অন্তর্বর্তী সরকারও প্রথম ক্রমিকে উল্লেখ করা সেসব সংস্কার অনায়াসেই করে ফেলতে পারত, যার চাপে ভবিষ্যতে জনরায়ের বৈধতা নিয়ে নির্বাচিত সরকার এলেও সংবিধান সংস্কারের মতো মৌলিক প্রশ্নগুলো অনিবার্য হয়ে উঠত।
অচিরেই আমরা একটি বিপুল অক্ষম বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে পাব, ‘জনসংখ্যার ডিভিডেন্ড’ ব্যবহার করতে না পেরে কোনো সঞ্চয় ছাড়াই যারা বুড়ো হবে। কয়েক বছর ধরে ট্রাফিক সিগন্যালে হাত পাততে থাকা বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমানতা তারই ইঙ্গিতবহ।
যেমন বেশ কটি গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে দুর্নীতি ও অপচয়ের মহামারির একটা বড় কারণ আমলাতান্ত্রিকতা। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেরই একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক। বিশ্বব্যাংকের ২৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ প্রকল্পের খরচ কীভাবে করা হবে, তার উদ্বেগজনক চিত্র মিলবে প্রথম আলোয় প্রকাশিত ‘বিশ্বব্যাংকেরasoxhsiuhs সিটা প্রকল্পের ব্যর্থতা ও অপচয়ের আশঙ্কা কেন’ শীর্ষক নিবন্ধটিতে। এই প্রকল্পের ১০ শতাংশের সামান্য বেশি ব্যবহার করা হবে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য, ১৩ শতাংশের কাছাকাছি ব্যয় করা হবে পরামর্শকের জন্য! অথচ নিবন্ধটির বিশেষজ্ঞ ও উদ্যোক্তা লেখকেরা দেখিয়েছেন, যা কেনা হবে, সেই সফটওয়্যার খাতে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক কম ব্যয়ে কাজটা করতে সক্ষম। এতে রক্ষণাবেক্ষণ খাতেও বিপুল ব্যয় থেকে দেশ বেঁচে যাবে! অথচ আড়াই শ মিলিয়ন ডলার পূর্বপরিকল্পনামতো ব্যবহৃত হলে সফটওয়্যার নির্মাণ খাতে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে ডেটা সিকিউরিটি হারাবে বাংলাদেশ।
উন্নয়নের নামে এ ধরনের অপচয়ই ছিল হাসিনা সরকারের অর্থনৈতিক ভিত্তি। অর্থনীতির সংস্কার যদি করতেই হয়, তাহলে এ ধরনের প্রকল্পগুলো আরও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে করা উচিত। প্রকল্পের খুঁটিনাটি তথ্য যদি না–ও দেওয়া যায়, তার মূল অংশগুলোকে বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম ও অংশীজনদের জন্য উন্মুক্ত রাখা সারা দুনিয়ার রীতি। অথচ এই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই পর্যালোচনার সুবিধার্থে সিটা প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশখ্যাত ব্যক্তিরাও ব্যর্থ হয়েছেন।
অন্তর্বর্তী সরকার বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে প্রকল্প গ্রহণ করছেন যথারীতি গোপনে, পুরোনো রীতিই অনুসরণ করে। অথচ আমলাতন্ত্রের বাইরে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিটি তৈরির মাধ্যমে এসব প্রকল্প যাচাই-বাছাইয়ের বন্দোবস্ত করে তারা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারত। এতে ভবিষ্যতের সরকারগুলোর পক্ষে সেই রীতি ভাঙা কঠিন হতো।
বাংলাদেশে দুর্নীতি আর অপচয়ের লাগামছাড়া পরিস্থিতির মস্ত কারণ মন্ত্রণালয়গুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে বিশেষজ্ঞদের কার্যকর ভূমিকা না থাকা। পৃথিবীর যে অল্প কিছু রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয়গুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জনপ্রশাসনের আমলারা প্রায় একচ্ছত্র ভূমিকা রাখেন, তার একটি বাংলাদেশ। পেশাদার কেউ তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্বে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন না।

ফিরোজ আহমেদ: রাজনীতিবিদ; সদস্য, সংবিধান সংস্কার কমিশনছবি: জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন বলে যে কমিশনটি গঠিত হয়েছে, তা–ও প্রধানত এই জনপ্রশাসনের ব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত হয়েছে। এর এক কৌতুককর পরিণতি হলো কৃষিবিদ কিংবা শিক্ষকেরা যখন কমিশনের কাছে তাদের বক্তব্য দিতে গেছেন, তাঁরা এই পেশাজীবীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, কৃষিবিদদের বক্তব্য তাঁরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে শুনবেন, শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য শুনবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। অর্থাৎ এই পেশাজীবীরা নিজেদের খাতে অজ্ঞানতা, অপচয় ও জবাবদিহির অভাবের জন্য যে মন্ত্রণালয়ের পর্যালোচনা করতে চান, অভিযোগকারীদের সংকট বিষয়ে শোনা হবে তাদের কাছ থেকেই।
অন্তর্বর্তী সরকার জনপ্রশাসনের আমলাদের বহুভাবে পুরস্কৃত করেছে, পুরোনো বন্দোবস্তকে নতুন করে পুষ্টি জুগিয়েছে।
৩.
অন্তর্বর্তী সরকারের কর্তব্য ছিল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ অন্তত দ্বিগুণ করার প্রক্রিয়া শুরু করা। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক গ্রেড বাড়ানো হয়েছে। এটাকে সামান্য উন্নতি বলা যেতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার মানদণ্ডেও শিক্ষকদের বেতন এরপরও অত্যন্ত কম। সত্যি বলতে কি, চাওয়ার সাহসও শিক্ষকেরা হারিয়ে ফেলেছেন। অন্তর্বর্তী সরকার এই খাতে রীতিমতো বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ রাখলে তা যে রাজনৈতিক সমর্থন পেত, তা বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে দিতে পারত।
বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটা মুক্ত তরুণ জনগোষ্ঠীকে আমরা পেয়েছি। নিপীড়ক শাসকেরা এই মুক্ত তরুণদের যে ভয় পায়, তা অকারণ নয়।
ফিরোজ আহমেদ, সদস্য, সংবিধান সংস্কার কমিশন
একই কথা প্রযোজ্য স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির জন্য। বাংলাদেশে বয়সের পিরামিড দ্রুত উল্টো হচ্ছে। অচিরেই আমরা একটি বিপুল অক্ষম বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে পাব, ‘জনসংখ্যার ডিভিডেন্ড’ ব্যবহার করতে না পেরে কোনো সঞ্চয় ছাড়াই যারা বুড়ো হবে। কয়েক বছর ধরে ট্রাফিক সিগন্যালে হাত পাততে থাকা বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমানতা তারই ইঙ্গিতবহ। কমে আসতে থাকা তরুণ জনগোষ্ঠী অচিরেই এদের ভার বহন করতে ব্যর্থ হবে। যে শ্রমিক জনগোষ্ঠী অকাতরে প্রাণ দিলেন, শুধু তাঁরাই নন, এই খাতে সংস্কার না হওয়ার পরিণামে মধ্যবিত্ত-জীবনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে।
পুলিশের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কও একটি বড় সংস্কারের বিষয় হওয়ার কথা ছিল। গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশের মধ্যেই সংস্কারের দাবি উঠেছিল। সাধারণ পুলিশ সদস্যরা প্রচারপত্র প্রকাশ করে তাঁদের জীবনের বঞ্চনার দিকটি জানান। পুলিশ সদস্যরা দাবি করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। মুক্তির কোনো সংবাদ দেখিনি। বিষয়টা একদম চাপা পড়ে গেছে।
অন্যদিকে খুব কম সভ্য রাষ্ট্রেই এতটা জবাবদিহিহীন পুলিশি ব্যবস্থা টিকে আছে। শুধু অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, গুম, খুন বা মামলার হয়রানি নয়, নাগরিকদের বিপদগ্রস্ত করা যেসব দুর্নীতির অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে আসে, তা কল্পনাতীত। প্রথম আলোতেই গত সরকারের আমলে শিরোনাম দেখেছিলাম, ‘মাছের রাজা ইলিশ, দেশের রাজা পুলিশ’। গণ-অভ্যুত্থানের চাপে এই মুহূর্তে হয়তো পুলিশ কিছুটা দমে আছে, কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এমন কোনো কাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, যা পরবর্তী সরকারকে পুলিশের বেপরোয়া ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারবে।
অন্তর্বর্তী সরকার হাসিনা আমলের নিন্দনীয় বহু আইনেরও লাগামছাড়া ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনটি তৈরি করা হয়েছিল উগ্রপন্থা দমনে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমাতে হাসিনার আমলে এই আইনের ঢালাও প্রয়োগ হয়েছিল। তার ধারাবাহিকতায় অন্তর্বর্তী সরকারও গোপালগঞ্জে ১০ হাজারের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে এই আইনে মামলা করেছে।
হতাশার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল, তেমন কোনো কার্যকর সংস্কার কোনো ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান নয়। এ কারণে ভবিষ্যতের চিত্র এখনই অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাঘনিষ্ঠ কারও কারও চাঁদাবাজি, দখল, দঙ্গল তৈরি করে হত্যা ও নিপীড়ন—এগুলো ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে স্বাভাবিক ঘটনায়।
৪.
২০২৪-এর বড় একটা সংস্কার অবশ্য গণ-অভ্যুত্থান নিজেই সম্পন্ন করেছে। সেটা হলো ‘গণরুম’ নামে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার উচ্ছেদ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীরা গণরুমের কাঠামোগত তাৎপর্য নিয়ে দৃশ্যত কোনো গবেষণা করেননি। আওয়ামী লীগের মতাদর্শিক আধিপত্যকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করা হলেও তার আসল গোমর কার্যত নিহিত ছিল শিক্ষার্থীদের ওপর বলপ্রয়োগের বন্দোবস্তে। সেটার কোনো রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত থাকলেও যাঁদের ওপর এই নিপীড়নের খাড়াটা ছিল, তারাই সেটাকে উচ্ছেদ করেছেন।
এর ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটা মুক্ত তরুণ জনগোষ্ঠীকে আমরা পেয়েছি। নিপীড়ক শাসকেরা এই মুক্ত তরুণদের যে ভয় পায়, তা অকারণ নয়। বিশ্ব-ইতিহাসের নানা পর্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, নিয়ন্ত্রণমুক্ত এমন তরুণেরা নতুন চিন্তা ও প্রবণতার জন্ম দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই দখলদারি কতটুকু ফিরে আসবে, শিক্ষার্থীরা একে কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারবেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে তার ওপর।
একটা সংগ্রামী জাতি নিজের প্রতি এবং অপরের চোখে মর্যাদা অর্জন করে। এটা সত্যি যে গণ-অভ্যুত্থানের এক বছরের মাথায় অজস্র হতাশা আমাদের ঘিরে ধরেছে। দঙ্গলের রাজত্ব আমাদের আতঙ্কিত করছে, না পাওয়ার বেদনা ক্রুদ্ধ করছে। কিন্তু সংবিধানের অধিকার নিয়ে, বিচার বিভাগের সংস্কার নিয়ে বা পুলিশের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক নিয়ে যে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহ দেশজুড়ে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, তা ছিল বিরল ছিল।
সত্যি বলতে কি, অভ্যুত্থানে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল ব্যাপক। বাংলাদেশের উপযুক্ত একটা সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির কাঠামোগত চেহারা নিয়ে কোনো গবেষণাও বাংলা ভাষায় প্রায় অনুপস্থিত ছিল। আমাদের এমন একটা গভীর আশাবাদ তৈরি হয়েছে যে ১৯৬০-এর দশকের পর আমরা আবারও একটা শক্তিমান বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী পাব, যারা আশু এবং দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল রূপান্তরের রূপরেখা কী হতে পারে, তা নির্মাণে শরীর ও মনকে যুক্ত করবেন।