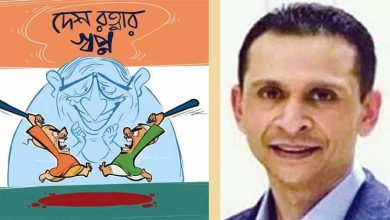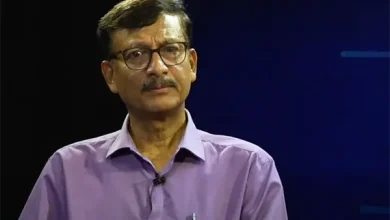জরিপের আড়ালে নির্বাচন-বিমুখতার কৌশলী ন্যারেটিভ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন এক মনস্তাত্ত্বিক খেলা শুরু হয়েছে— যার মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে জরিপ। নির্বাচন ঘিরে ভোটারদের আস্থা নষ্ট করা এবং বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে—এমন অভিযোগ তুলেছেন রাজনীতিসচেতন মানুষ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সম্প্রতি ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ও ‘ভয়েস ফর রিফর্ম’ যৌথভাবে প্রকাশিত ‘পালস সার্ভে ৩’ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সচেতন নাগরিক মহলে তীব্র আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
এই জরিপে দেখা গেছে, আগামী নির্বাচনে কাকে ভোট দেবেন—এই প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীন মানুষের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮.৫০ শতাংশে।
মাত্র আট মাস আগে (২০২৪ সালের অক্টোবর) এই ছিল ৩৮ শতাংশ। কাকে ভোট দেবেন, তা বলতে চান না ১৪.৪০ শতাংশ, আর সরাসরি ভোট দেবেন না বলেছেন ১.৭০ শতাংশ।
দলভিত্তিক সমর্থনের চিত্রেও এসেছে বড় পরিবর্তন। বিএনপির ভোট ১৬.৩০ শতাংশ থেকে নেমে ১২ শতাংশ, জামায়াতের ১১.৩০ থেকে ১০.৪০ শতাংশ, আর এনসিপির ভোট ২ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ২.৮০ শতাংশ হয়েছে।
নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ভোটও ৮.৯০ থেকে নেমে ৭.৩০ শতাংশ। অন্যান্য ইসলামী দলের ভোট নেমে এসেছে ০.৭০ শতাংশে।
তবে প্রশ্নটি উল্টো করে—‘আপনার এলাকায় কোন দলের প্রার্থী জিতবে বলে মনে হয়?’—জিজ্ঞেস করলে ৩৮ শতাংশ বিএনপির, ১৩ শতাংশ জামায়াতের, ১ শতাংশ এনসিপির এবং ৭ শতাংশ আওয়ামী লীগের নাম বলেছে। এর মাধ্যমে বর্তমান প্রেক্ষাপটেও আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে।
জরিপে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ কমেছে। অক্টোবরের তুলনায় রাজনৈতিকভাবে দেশ সঠিক পথে আছে বলে মনে করা মানুষের হার ৫৬ শতাংশ থেকে নেমে ৪২ শতাংশে এসেছে। তবে অর্থনৈতিকভাবে সঠিক পথে আছে বলে মনে করা মানুষের হার ৪৩ থেকে বেড়ে ৪৫ শতাংশ হয়েছে।
সংস্কারনির্ভর ভোটের দাবি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে—৫১ শতাংশ বলেছে ‘ভালোভাবে সংস্কার করে তারপর নির্বাচন’, ১৭ শতাংশ চায় ‘কিছু জরুরি সংস্কারের পর নির্বাচন’, আর মাত্র ১৪ শতাংশ চায় ‘সংস্কার বাদ দিয়ে নির্বাচন’।
প্রয়োজনীয় সংস্কারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে— আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন (৩০%), দুর্নীতি দমন (১৭%), আইন ও বিচারব্যবস্থার উন্নতি (১৬%), অর্থনীতি চাঙ্গা করা (১৬%), নিত্যপণ্যের দাম কমানো (১৩%), রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অসহনশীলতা কমানো (১৯%) এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার (১৯%)।
যদিও ৭০ শতাংশ মানুষ মনে করে, আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে—১৫ শতাংশ এর বিপক্ষে মত দিয়েছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই জরিপ শুধু তথ্য দেয়নি, বরং এক কৌশলী ন্যারেটিভ দাঁড় করিয়েছে, যাতে একদিকে ভোটের আগ্রহ কমিয়ে দেখানো হচ্ছে, অন্যদিকে বিএনপি, জামায়াতের মতো রাজনৈতিক শক্তির জনপ্রিয়তাকে খাটো করে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হলো, বিগত শাসনামলে সংঘটিত সীমাহীন দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড—এসবের বিচার নিয়ে জনগণের অবস্থান জরিপে একেবারেই অনুপস্থিত।
বিআইজিডির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দৈনিক বণিক বার্তার এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের গবেষণা সেল সিআরআইয়ের সঙ্গে আসিফ সালেহ যুক্ত ছিলেন। সিআরআই শুধু নীতি-পরামর্শই দেয়নি, বরং বিরোধী মত দমনে অপপ্রচার ছড়ানোর অভিযোগও রয়েছে।
যদিও আসিফ সালেহ পরে ফেসবুকে স্পষ্ট করেন— তিনি রাদওয়ানের ‘পরামর্শক পরিষদের সদস্য’ নন, তবে স্বীকার করেন ২০২০ সালে সিআরআই সংশ্লিষ্ট হোয়াইট বোর্ড পলিসি ম্যাগাজিনে তিনি সামাজিক সেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটি লেখা দেন। তাঁর দাবি, এটি ছিল সম্পূর্ণ ‘নির্দলীয়’ ভূমিকা।
তবু প্রশ্ন রয়ে যায়, যে প্রতিষ্ঠান সরাসরি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে, তার সঙ্গে যুক্ত থেকে কতটা নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব? আর সেই প্রভাব কি এই জরিপের ফলাফল ব্যাখ্যায় ভূমিকা রাখেনি?
এ ধরনের তথ্যবহুল কিন্তু অসম্পূর্ণ জরিপ জনগণের মধ্যে ভোট ও গণতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই চালানো হতে পারে। নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার পরিকল্পিত কৌশল এটা।
গণতন্ত্রের শক্তি হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণ ও ভোটের মর্যাদা। এ ধরনের প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং নির্বাচনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হতে হবে।
সব মিলিয়ে এই জরিপ কেবল ভোটের হার বা দলের জনপ্রিয়তার তথ্য দেয়নি, বরং এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি করেছে, যা আগামী নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ও জনগণের মনোভাব প্রভাবিত করার সরাসরি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা কি না, সেই প্রশ্ন এখন জনমনে। সচেতন নাগরিকদের ভাষায়, ‘গবেষণার ছদ্মবেশে গণতন্ত্রবিরোধী প্রোপাগান্ডা’।