ভারতের ডিজাইনে ফের ‘হাসিনা শাসন’?
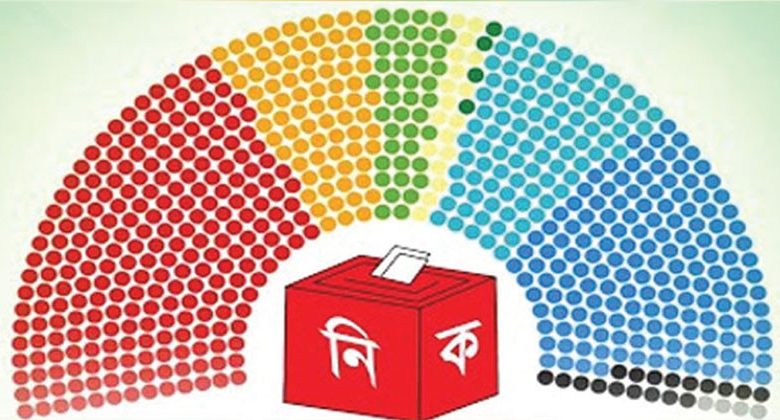
সংখ্যানুপাতিক আসন-তত্ত্ব তছনছ হবে অলিখিত বন্দোবস্ত * পি.আর.পদ্ধতির আলোচনা ভিত্তিহীন
হাসিনামুক্ত বাংলাদেশ যখন একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য উন্মুখ তখন মাঠে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন-তত্ত্ব। সংক্ষেপে যাকে পি.আর. পদ্ধতির (প্রোপোর্শনাল রেপ্রেজেন্টেশন) নির্বাচন বলা হচ্ছে। পি.আর.পদ্ধতির জিগির আকস্মিকভাবে মাঠে ছাড়া হয় গত ২৮ জুন। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন’র ব্যানারে ওইদিন একটি মহাসমাবেশ হয়। ওই সমাবেশে প্রধান ভোকাল ছিলো জামায়াতে ইসলামী। দলটির ঢাকা সমাবেশে আরো মঞ্চে ওঠেন নবগঠিত ‘ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), নেজামে ইসলাম পার্টি, হিন্দু মহাজোট, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ, গণঅধিকার পরিষদ,বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, খেলাফত আন্দোলনসহ ছোট-বড় অন্ততঃ ১০ সংগঠনের নেতা। মঞ্চে ছিলেন না দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি’র কোনো নেতা। ছিলেন না বিএনপি’র সমমনা অনেক রাজনৈতিক দলই। বিশ্লেষকরা এ সমাবেশকে ই.শা’র ব্যানারে জামায়াতের মহাসমাবেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। জামায়াতের পরিকল্পনা ও দাবিগুলোই বক্তাদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে তত্ত্ব মাঠে ছাড়া হয়েছে সেটি কতটা বাস্তবসম্মত ? বিদ্যমান শাসন কাঠামো, নির্বাচনী আইন (আরপিও) এবং সংবিধান কী বলে ? যে রাজনৈতিক নতুন বন্দোবস্তের আকাক্সক্ষায় জুলাই-আগস্টের রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে- সেই আকাক্সক্ষারই বা কতটা প্রতিফলন রয়েছে এতে ? নাকি সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন দাবির মোড়কে দেশকে পুনরায় এক নায়ক ও মাফিয়াতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে নিপতিত করার ভারতীয় এজেন্ডারই বাস্তবায়নের প্রয়াস চলছে ? এমন প্রশ্ন তুলেছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ, আইনজ্ঞ, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
পি.আর. পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবির ভালো-মন্দ জানতে চাওয়া হলে সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন, মানুষ এখন জাতীয় নির্বাচনের জন্য উন্মুখ। এ মুহূর্তে পি.আর. পদ্ধতির নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। কিভাবে নির্বাচন হবে সেটি নির্বাচনী আইনে বলা আছে। সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকতেও এ নতুন এ বিতর্ক সামনে আনা হচ্ছে একটি মাত্র কারণে। সরকারে এখন যারা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে চান। যাতে জবাবদিহিতার সরকার গঠিত না হয়। জাতীয় নির্বাচন যাতে পিছিয়ে যায়। এই আলাপ এখন অর্থহীন।
তার মতে, নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে যারা পরিবর্তন আনতে চান তারা সরকার গঠন করে সেটি করুন। অন্তর্বর্তী সরকার কেন এটি করবে ? এটি তাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে না।
মনজিল মোরসেদ বলেন, এখন তরুণদের যুগ। তাদের গায়ে জোর আছে। আমরা বয়স্করা শুধু বলতেই পারবো। পি.আর. পদ্ধতির নির্বাচন নিয়ে এখনকার আলোচনা ভিত্তিহীন। নির্বাচন পদ্ধতি একটি সামাজিক চুক্তি। যারা চাইছেন তারা ক্ষমতায় গিয়ে যদি এটি করেন তাহলে ঠিক আছে। আলোচনার ভিত্তিতে এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটতে পারে না। আমরা নব্বইতে দেখেছি এমন আলোচনা। দল ক্ষমতায় গিয়ে সেই ঐকমত্যের মূল শর্তটিই পূরণ করেনি।
সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, পি.আর. পদ্ধতিটিই আমার কাছে পরিষ্কার নয়। এখন যারা মাঠের রাজনীতিতে আছেন তারা সবাই চাইলেও যদি বিএনপি না চায় সেটি বাস্তবায়ন হবে না। ঐকমত্য না হলে কিভাবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন হবে?
তিনি বলেন, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন ঐকমত্য কমিশন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। যে ক’টি ইস্যুতে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবে না সেসব ইস্যুতে গণভোট দিতে পারেন। গণভোট দিতে হলে সেটি ফেব্রুয়ারির আগেই দিতে হবে। দলগুলো ঐকমত্যে না পৌঁছলে পি.আর. পদ্ধতির আলোচনার কিছু যায় আসে না। তিনি বলেন, দলগুলোর মধ্যে যদি মেজর ইস্যুতে ঐকমত্য না হয় তাহলে হয় জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। অন্যথায় অমীমাংসিত বিষয়ে গণভোট করতে হবে। বর্ষীয়ান এ আইনজীবী সংবিধান স্থগিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ব্যক্ত করেন।
এদিকে জামায়াত বা ই.শা.আন্দোলনের মঞ্চে উঠে পি.আর. পদ্ধতির নির্বাচন দাবিকারী সংগঠনগুলো কি বুঝে সংখ্যানুপাতিক হারে আসনের ভাগ-বাটোয়ারা চাইছেন সম্প্রতি তার একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন প্রবাসী লেখক, জনপ্রিয় অ্যাক্টিভিস্ট ডা: পিনাকী ভট্টাচার্য। দাবিটির পক্ষ কিংবা বিপক্ষে মতামত না দিয়ে তিনি শুধু কিছু বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, বিএনপি ছাড়া সব দল চায় পি.আর. পদ্ধতির নির্বাচন। কেন চায়, কিংবা কেন চায় না এটি কেউ বলতে পারবে না। বিএনপি কেন চায়না এটিও কেউ বলতে পারবে না। জামায়াতও না। তার মতে এটি হচ্ছে ফ্যাসিবাদের নতুন ক্যারিশমা। যার পরিকল্পনায় রয়েছে ভারত।
তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, পদ্ধতিটি দেশের জন্য ভালো হবে কি ? কি বুঝে রাজনৈতিক দলগুলো পি.আর. পদ্ধতির পক্ষে কিংবা বিপক্ষে বলছে ? এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে কি ? রাজনৈতিক দলগুলো কি বুঝে পি.আর. চাইছে আর কি বুঝে চাইছে না- সেটি কেউ এখনো বুঝে উঠতে পারেননি।
হাসিনা পালানোর পরপর জামায়াত ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলো। এটির মধ্যে ইন্টারেস্টিং বিষয় ছিলো ‘সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন’। অর্থাৎ মোট ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে আসন ভাগাভাগি। নির্বাচনে যে দল যতগুলো ভোট পাবেন সেই অনুপাতে তাদের মধ্যে সংসদের ৩শ’ আসন ভাগ বাটোয়ারা হবে।
ধরা যাক, একটি আসনে মোট ভোটার ১০ লাখ। নির্বাচন হলো। ভোটে বিএনপি পেলো ৫ লাখ। জামায়াতে ইসলামী পেলো ৩ লাখ। কথার কথা, আ’লীগ পেলো ১টি ভোট। তাও চূড়ান্ত গণনা যদি এটি টেকে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে বেশি ভোট পাওয়ায় বিএনপিকেই ‘জয়ী’ ঘোষণা করা হলো। এখন জামায়াত যে ৩ লাখ ভোট পেলো, বিদ্যমান পদ্ধতিতে এটিতো পুরোটাই লোকসান। কিন্তু না। জামায়াত বলছে, সারাদেশে যত ভোট পড়বে অর্থাৎ ৩শ’ আসনে যত ভোট পড়বে তার মধ্যে ওই দল যত শতাংশ পাবে সেই অনুপাতে আসন ভাগাভাগি করতে হবে।
সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হলে জামায়াত যদি ৩ লাখ ভোটও পায় তবুও সে সংখ্যানুপাতে আসন পাবে। তার মানে কোনো সিটে যারা পৃথকভাবে জিততে পারবে না তারা যদি সারাদেশের মোট ভোট মিলিয়ে একটি পার্সেন্টেজে আসে তাহলে সেই পার্সেন্টেজ অনুপাতে ওই দলকে আসন দিতে হবে। এ হিসেবে কোনো রাজনৈতিন দল যদি সারাদেশে এক শতাংশ ভোটও পায় তাহলে তারা ৩শ’ আসনের মধ্যে ৩টি সিট পাচ্ছে। যতি অর্ধ শতাংশ ভোটও পায় তাহলে অন্ততঃ একটি আসন পাবে। ছোট দলের জন্য এ পদ্ধতি খারাপ নয়। তারাও ন্যূনতম একটি করে সিট পাবে।
ইউরোপের অনেক দেশে এই সিস্টেম আছে। ছোট দলগুলোর জন্য এটি ভালো। জাতীয় রাজনীতিতে ছোট দলেরও একটি ভয়েস রয়েছে। কিন্তু ইউরোপে আছে বলেই কি বাংলাদেশের জন্য সেটি ভালো ? পশ্চিমা রাজনীতিতো অনেক কিছুই আছে। পশ্চিমা রাজনীতি থেকে কি আমরা সেকুলারিজম এনেছি ? পশ্চিমে এলজিবিটি রাইটস আছে। আমরা কি সেটি নিয়েছি ? আমাদের মানুষ এলজিবিটি রাইটস মেনে নেবে ? পশ্চিমে মদ খাওয়া। জুয়া খেলা। ক্যাসিনো বৈধ। আমাদের দেশের মানুষ কি এসব মেনে নেবে ?
তার মানে পশ্চিমে আছে বলেই এটি কোনো ‘সাফাই’ হতে পারে না। ছোট দলের জন্য পি.আর. সিস্টেম ভালো। প্রশ্ন হচ্ছে, জামায়াত কি ছোট দল ? জামায়াত কি চিরদিনের জন্য ‘ছোট দল’ই থেকে যাবে ? দেখা উচিৎ সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ কি না। করলে কেন করা উচিৎ ? না করলে কেন করা উচিৎ নয় ?
বিদ্যমান নির্বাচনে মানুষ প্রার্থীকে ভোট দেয় না। প্রতীককে ভোট দেয়। প্রতীকের পক্ষে প্রার্থী ভোট চাইতে গিয়ে প্রার্থী হয়তো বলেন, আমার দলকে ভোট দিলে আমরা এই এই উন্নয়ন কার্যক্রম করবো। ব্রিজ-রাস্তা করে দেবো। পথ-ঘাট বানিয়ে দেবো।
কিন্তু কেন ছোট দলগুলো পি.আর. পদ্ধতি চায় সেটি দেখা যাক। দলীয় ডকুমেন্ট থেকে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। জামায়াতের ডকুমেন্ট কি বলে ?
সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চাওয়া দলগুলোর মধ্যে জামায়াত সবচেয়ে বড় দল। তাদের দাবির পক্ষে কী যুক্তি দিচ্ছে সেটি বোঝার বিষয়। জামায়াতের সাবেক আমীর গোলাম আযম ২০০৫ সালে একটি বই লেখেন। ‘জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি’। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন নিয়ে বইটিতে প্রায় সবগুলো আর্গুমেন্ট রয়েছে। তবে বইটির তিন নম্বর প্যারায় পটভূমিতে গোলাম আযম সংখ্যানুপাতের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন, সিপিবিও নাকি সংখ্যানুপাতিক ভোটের পক্ষে। অথচ সিপিবি সংখ্যানুপাতিক ভোট চাইলে জামায়াতের জন্য এটি হারাম হওয়া উচিৎ। কিন্তু হয়নি। সিপিবি চেয়েছে বলে জামায়াতও সেটি গর্বভরে চাইছে। জাতীয় পার্টির এরশাদও নাকি সংখ্যানুপাতিক ভোট চেয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সিপিবি এবং জাতীয় পার্টির চেয়ে বড় ভারতীয় তল্পিবাহক কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেউ আছে ? নেই। এরশাদ এবং সিপিবি যেটি একসঙ্গে চায় এটি যে ভারতেরই চাওয়া এটি বোঝার জন্য কি দার্শনিক হওয়ার প্রয়োজন আছে ? এটি ভারতীয় পলিসি। সহজ সমীকরণ এটি।
বইটির ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় গোলাম আযম বলেন, প্রচলিত রাজনীতি হলো পাওয়ার পলিটিক্স বা ক্ষমতার রাজনীতি। দেশ গড়া নাকি আসল লক্ষ্য নয়। ক্ষমতাসীন হওয়াই নাকি আসল লক্ষ্য। অর্থাৎ ‘ক্ষমতা’ জামায়াতে ইসলামীর কাছে খুব খারাপ জিনিস ! অথচ রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ক্ষমতা। ক্ষমতায়িত হওয়ার জন্যই দলগুলো রাজনীতি করে। এই সহজ কথাটি জামায়াত স্বীকার করে না। এ কারণেই বলা হয়, জামায়াত এখনো কোনো রাজনৈতিক দল হয়ে উঠতে পারেনি। কল্পনার বাংলাদেশ সব নাগরিকই দেখে। আমাদের সকলের ইমাজিনেশনের বাংলাদেশ আলাদা। জামায়াতেরও একটি ইমাজিনেশন আছেন। বিএনপি যারা করেন তাদের ইমাজিনেশন কি জামায়াত সমর্থকদের ইমাজিনেশনের সঙ্গে মিলবে ? জামায়াত যে ইমাজিনেশনে বিশ্বাসী সেটি বাস্তবায়ন করতে হলেও হাতে ক্ষমতা লাগবে। জামায়াতে ইসলাম কি তাহলে ক্ষমতায় আসতে চায় না? রাজনীতি মানেই হচ্ছে ক্ষমতার প্রশ্ন। রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা সংক্রান্ত কৌশলগত ক্ষেত্র। রাজনীতি দিয়ে ক্ষমতা তৈরি হয়। জামায়াত যেটিকে ‘দেশ গড়া’ বলে। আওয়ামীলীগের কাছে সেটি ‘দেশ ধ্বংস করা’। ‘দেশ গঠন’ কোনো রাজনৈতিক শব্দ নয়। এটি সাহিত্যের ভাষা।
জামায়াত সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে একটিই যুক্তি দিচ্ছে। সেটি হচ্ছে, টাকার খেলা বন্ধ করা। প্রার্থীদের টাকা খরচ করতে হয়। বিষয়টি আপাতঃ মনে হচ্ছে খুব স্বচ্ছ। কিন্তু ধরুন জাতীয় পার্টি। অনেকের দৃষ্টিতে এটি ‘খারাপ’ দল। এ দলও নির্বাচনে ৭ শতাংশ ভোট পায়। সংখ্যানুপাতিক হলে জাতীয় পার্টি ২১টি আসন পাবে। ২১টি না পেলে ১৫টি পাবে। কিংবা তার চেয়েও কম কিংবা ৫টি পেলো। এর মধ্যে জাতীয় পার্টি যদি একেকটি আসন ৫শ’ কোটি টাকায় বিক্রি করতে চায় সেটি কি বিক্রি সম্ভব নয় ? হতেই পারে। আপস-রফার মাধ্যমেই কিনে নেবে। আওয়ামীলীগের লোকেরাই কিনে নেবে। এলাকায় যেতে হলো না। মারপিট করতে হলো না। ভোট কেন্দ্র দখল করতে হলো না। এমনকি রাজনীতিও করতে হলো না। নমিনেশন কিনতে হলো না। কারণ নমিনেশন বাণিজ্যও অনেক দল করে। কারো টাকা আছে। জাতীয় পার্টির জয়লাভ করা আসন আ’লীগ কিনে নিলো ! কোনো ঝুঁকি নেই। পরাজয়ের কোনো ভয় নেই। ধরা যাক দলগুলো আসন ভাগ করে নিলো। এখন যেভাবে আছে। ধরা যাক, রংপুর। রংপুরে যতগুলো কেন্দ্র আছে সেখানে যদি জাতীয় পার্টি জয়লাভ করে। আর আগে থেকেই যদি সংশ্লিষ্ট এমপি প্রার্থীর সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া থাকে যে, ওইসব আসনে দলের যে-ই জিতুক সেখানে নির্দিষ্ট একজনকেই এমপি করা হবে। তাহলে যিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি হলেন তিনি কি ওই আসনে টাকা খরচ কবেন না ? তাহলে টাকার খেলা কমলো কি করে ? বরং বাড়লো টাকার খেলা। টাকার খেলাকে আরো কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হলো। কারণ জনগণ তখন ওই প্রার্থীকে ভোট দেবে না। ওই আসনে কে প্রার্থী হবেন এটি ঠিক করবেন দলের নেতা।
সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনে আর কি কি সমস্যা ? দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। নেতৃত্ব অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে দলীয় তালিকা তৈরি হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিত্বকে দুর্বল করে দেবে। দলীয় নেতৃত্ব ক্ষমতাকে আরো কেন্দ্রীভূত করবে। স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা কমবে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবে- কে সংসদে যাবে। ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটের ক্ষমতা কমে যাবে। এখনতো জনপ্রিয় নেতা হলে জেতার সুযোগ রয়েছে। অন্ততঃ মানুষের কাছে ভালো হতে হয়। পি.আর. পদ্ধতিতে সেটির কোনো দরকারই পড়বে না। আমরা অনেকে মনে করি, রাজনীতি মানে হলো নির্বাচন। আইন, সংসদ। কিন্তু রাষ্ট্র বিজ্ঞানী মুসতাক আহমেদ একটি মজার কথা বলেন। তিনি বলেন, রাজনীতি মানে হচ্ছে এক অদৃশ্য বোঝাপড়া। যেটিকে বলা হয় রাজনৈতিক বোঝাপড়া। বা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। যেটিতে ঠিক হয় কে ক্ষমতায় থাকবে। কে টাকা খাবে। আর কে নিরাপদে থাকবে। এই বোঝাপড়াটাকেই বলা হয় পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট বা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। ছাত্ররা জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই বন্দোবস্তটা ভাঙতে চেয়েছিলেন। যেটিকে বলা হচ্ছে, ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত’। এটি কোনো লিখিত বন্দোবস্ত নয়। অথচ বাস্তব ও কার্যকর। বড় বড় রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, আমলা, পুলিশ, বিচারক সবাই এ অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে।
রাস্তার ট্রাকের চান্দাবাজি। বাজারে ইজারা, ব্রিজের টোল, বালু মহাল, ছিনতাই, মাস্তানি। এসব বিষয় দিয়ে টাকা-পয়সা আসে। এসবের একটি ইকনোমি আছে। কে তুলবে টাকা। টাকা তুলে কাকে দেবে। পুলিশ কত পাবে। রাজনৈতিক নেতা কত পাবে। মাস্তান কত পাবে। মন্ত্রী কত পাবে। হাসিনা কত পাবে। সব কিছু স্যাটেলড। উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সেটিই অলিখিত চুক্তির আওতায় তারা এটি পায়। এটিকেই বলে বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের অংশ হচ্ছেন এমপি। তিনি মাস্তান পালেন। কর্মী পোষেন। পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখেন। স্থানীয় মাফিয়া বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রাখে। এইভাবে এ বন্দোবস্ত টিকে থাকে। হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর অপরাধ বেড়েছে কেন ? এই আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিলো তারা এখন নেই। এখন কেউ সেভাবে কন্ট্রোল করে না। তারা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যা খুশি করছে। এটি ল অ্যান্ড অর্ডারের বিষয় নয়। এটি সেই অলিখিত চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার পরিণতি। আমাদের একটি নতুন বন্দোবস্তের কায়েমের আগেই জামায়াতের মতো রাজনৈতিক দল নতুন বন্দোবস্ত ভাঙছে।
রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সেইরকম ইনস্টিটিউট নেই। গড়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতির বিকল্প হচ্ছে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। এইখাতে রাজনৈতিক দল, নেতা-কর্মী একটি জটিল ভারসাম্য রক্ষা করে সমাজ টিকিয়ে রাখে। এটি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তখন সহিংসতা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে যায়। অস্থিরতা বাড়ে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন করে পুরো রাজনৈতিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। রাজধানীর আন্ডারওয়ার্ল্ডই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য, ভাগ-বাটোয়ারা-এ স্থানটি কার নিয়ন্ত্রণে যাবে ? সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন দিয়েতো সব অলিখিত বন্দোবস্ত ওলোটপালোট করে দেয়া হলো। সেই স্থানটি কে নেবে ? পুলিশ নেবে। প্রশাসন নেবে। আরেকটা ‘হাসিনা শাসন’ তৈরি হবে। রাষ্ট্র রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। অলিখিত বন্দোবস্তই সমাজকে টিকিয়ে রাখে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন দিয়ে সেই কাঠামো ভাঙার গুগলি মারলে রাষ্ট্র গড়িয়ে পড়বে গ্যাঙয়ের হাতে। পুলিশের হাতে প্রশাসনের হাতে। স্থানীয় মাফিয়ার হাতে।
তালেবান শাসন ক্ষমতায় আসার আগে আফগানিস্তানে এমন হয়েছিলো। একেক এলাকা একেক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করতো। বাংলাদেশে একই ঘটনা ঘটবে। পুলিশ আর প্রশাসন দারুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন আঞ্চলিকতা বাড়িয়ে দেবে। ডা: পিনাকী এ প্রসঙ্গে বেলজিয়াম এবং ইসরাইলের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেন।







